বর্বর অভিযান এবং রোম সাম্রাজ্যের পতন

বিশ্ব ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের উত্থান যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তার পতনও এক গভীর রহস্য এবং শিক্ষার বিষয়। প্রায় পাঁচ শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আইন, স্থাপত্য, সামরিক কৌশল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রোমানদের যে অনন্য অবদান, তা আজও আধুনিক বিশ্বে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যত বড়ই সাম্রাজ্য হোক না কেন, এক সময় তা পতনের দিকে যেতেই পারে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে বহু জটিল কারণ থাকলেও বর্বর জাতিগুলোর অব্যাহত অভিযান ছিল এর চূড়ান্ত পরিণতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক।
রোম সাম্রাজ্যের শক্তির শিখরে পৌঁছানোর পরেও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বারবার সম্রাট পরিবর্তনের মতো ঘটনাগুলো সাম্রাজ্যকে ভেতর থেকে দুর্বল করে তুলেছিল। তৃতীয় শতাব্দীর ‘Crisis of the Third Century’ নামে পরিচিত সময়কালটি ছিল এক সংকটময় সময়, যেখানে বিভিন্ন সামরিক নেতা রোমের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হন। এই সময়ে রোমে প্রায় ২৬ জন সম্রাট শাসন করেন, যার অধিকাংশই সেনাবাহিনীর দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন বা নিহত হন। এর ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।
এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ইউরোপের উত্তরের বর্বর জাতিগুলো ধীরে ধীরে রোমের সীমান্তে অনুপ্রবেশ শুরু করে। ‘বর্বর’ শব্দটি রোমানদের দৃষ্টিতে সেইসব জাতিগুলোর জন্য ব্যবহৃত হত, যারা রোমান ভাষা, সভ্যতা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এদের মধ্যে গথ, হান, ভ্যান্ডাল, ফ্র্যাঙ্ক, লোম্বার্ড, আলান, সুয়েবি প্রভৃতি জাতিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব বর্বর গোষ্ঠী প্রথমদিকে রোমান সীমান্তে আক্রমণ চালালেও পরবর্তীতে তারা রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ভূখণ্ড দখল করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিছু গোষ্ঠী আবার রোমান সাম্রাজ্যের সৈন্য হিসেবে নিযুক্ত হয়ে অভ্যন্তরীণভাবে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে।
রোম সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করার ঘটনাও এর পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিস্তি হিসেবে বিবেচিত। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়ুস মৃত্যুবরণ করার পর সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে ভাগ করে দুই পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বহু শতাব্দী টিকে থাকলেও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য দ্রুত দুর্বল হতে থাকে এবং বর্বরদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।
এই প্রেক্ষাপটে বর্বর আক্রমণগুলোর তাৎপর্য বোঝা যায় এক গভীর ইতিহাস-চিন্তার মাধ্যমে। বর্বররা শুধুমাত্র যুদ্ধবাজ ও ধ্বংসাত্মক ছিল না, বরং তারা ধীরে ধীরে রোমান প্রশাসন, আইন ও সামরিক কৌশলের অংশ হয়ে ওঠে। তারা কেবল রোমকে আক্রমণ করেনি, বরং রোমের অবশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোকে নিজেদের উপযোগে রূপান্তর করে নতুন ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে।
এই প্রথম ধাপে, আমরা রোমের ঐতিহাসিক গৌরব, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, বর্বর জাতিগুলোর বিকাশ ও সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। পরবর্তী ধাপে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব – কোন কোন বর্বর গোষ্ঠী কখন এবং কিভাবে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে, এবং কীভাবে তারা রোমের পতনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
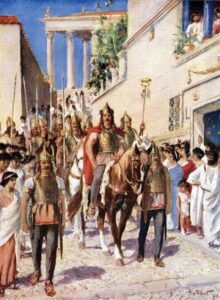
রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বর্বর জাতিগুলোর আগমন এক বিশাল বাঁক। তারা শুধু বহিরাগত শক্তি হিসেবেই আবির্ভূত হয়নি, বরং ধীরে ধীরে রোমের অভ্যন্তরেই এক অশান্ত অস্থিরতার জন্ম দেয়, যার শেষ অধ্যায় ছিল সাম্রাজ্যের পতন। বর্বর আক্রমণ বলতে শুধু কিছু যোদ্ধা গোষ্ঠীর আগমন বোঝায় না, বরং এটা ছিল এক চলমান জনগোষ্ঠীর বিস্ফারণ, স্থানান্তর এবং সামরিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সংঘর্ষ। বিশেষ করে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এদের কার্যকলাপ রোমান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের উপর এক স্থায়ী ছাপ ফেলে।
প্রথম উল্লেখযোগ্য বর্বর গোষ্ঠী ছিল গথ। গথেরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—ভিসিগথ এবং অষ্ট্রোগথ। চতুর্থ শতকের শেষ দিকে, হুনদের তীব্র আগ্রাসনের কারণে ভিসিগথরা দানিউব নদী অতিক্রম করে রোমান ভূখণ্ডে আশ্রয় চায়। শুরুতে রোমানরা তাদের অনুমতি দিলেও শরণার্থীদের প্রতি নির্যাতন ও দুর্যোগপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে তারা রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ culminate হয় ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দের অ্যাড্রিয়ানোপল যুদ্ধ-এ, যেখানে ভিসিগথরা রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ভ্যালেন্সকে হত্যা করে এক ভয়াবহ পরাজয়ের স্বাদ দেয়। এই যুদ্ধে রোমান সামরিক শক্তির উপর যে আঘাত আসে, তা সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার ক্ষমতাকে চিরতরে দুর্বল করে দেয়।
এই ঘটনার কয়েক দশক পর, ৪১০ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথদের নতুন নেতা অলারিক রোম নগরীতে প্রবেশ করে এবং তিন দিনব্যাপী ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। প্রায় আটশো বছরের মধ্যে রোম নগরী এটাই প্রথমবার কোনো বিদেশি জাতির হাতে পড়ে। এই ঘটনাটি কেবল সামরিক দিক থেকে নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও বিশাল ধাক্কা ছিল, কারণ রোমকে মানুষ তখনো “অজেয় ও চিরন্তন শহর” বলে ভাবত।
গথদের পরে ইতিহাসে প্রবেশ করে এক ভয়ংকর যোদ্ধা জাতি—হুন। এশিয়ার অভ্যন্তর থেকে আগত এই জাতি অদম্য ঘোড়সওয়ার, নিষ্ঠুর ও বর্ণনাতীত রকমের ভীতিপ্রদ ছিল। তাদের নেতা আটিলা দ্য হান, যিনি নিজেকে ‘ঈশ্বরের দণ্ড’ বলতেন, পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপজুড়ে এক আতঙ্কের প্রতীক হয়ে ওঠেন। হুনদের আক্রমণের ফলে শুধু রোম নয়, বর্বর জাতিগুলোও নিজেদের সীমানা ও অবস্থান পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হয়। ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাটালাউনিয়ান ফিল্ডস নামক এক ভয়াবহ যুদ্ধে রোমান ও ভিসিগথ মিত্রবাহিনী আটিলাকে পরাজিত করে, যদিও এটি হুনদের দমন করে পুরোপুরি শেষ করে না।
ভ্যান্ডাল জাতিও এক বিশিষ্ট বর্বর গোষ্ঠী ছিল যারা মূলত মধ্য ইউরোপ থেকে পশ্চিম ইউরোপ ও পরে উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। তারা ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে কার্থেজ দখল করে রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। পরে ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে তারা সরাসরি রোম নগরী আক্রমণ করে এবং এক ভয়াবহ লুটপাট চালায়। এখান থেকেই ইংরেজি শব্দ “vandalism”-এর উৎপত্তি, যার অর্থ আজ ধ্বংস বা নষ্ট করে ফেলা।
একই সময়ে সুয়েবি, আলান, বুর্গুন্ডিয়ান, লোম্বার্ড প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলোও রোমান ভূখণ্ডে বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালাতে থাকে। ৪০৬ খ্রিস্টাব্দে তারা একযোগে রাইন নদী অতিক্রম করে গল প্রদেশে প্রবেশ করে, যা রোমের সীমান্ত প্রতিরক্ষাকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। এই ঘটনার ফলেই ইউরোপের এক নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হতে থাকে—বর্বর জাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্য ও অঞ্চল ক্রমশ বিস্তৃত হয়।
এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বর্বরদের মধ্যে অনেকে কেবল দখলদার হিসেবে আসেনি, বরং তারা রোমান প্রশাসনের ভেতরেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। কিছু বর্বর গোষ্ঠীকে রোম “ফোএডেরাটি” (Foederati) বা মিত্র হিসেবে সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের দেওয়া হয় জমি, নাগরিক সুবিধা, এমনকি উচ্চপদস্থ সামরিক পদ। এর ফলে রোমান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বেও বর্বরদের স্থান নিশ্চিত হয়। একপর্যায়ে এই বর্বর নেতারাই রোমান রাজনীতির চাবিকাঠি ধরে নেয় এবং সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করতে থাকে।
রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পঞ্চম শতাব্দী ছিল সর্বাধিক সংকটাপন্ন এক সময়, যখন একের পর এক বর্বর গোষ্ঠী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করে নেয় এবং সাম্রাজ্যটিকে কেন্দ্র থেকে ধ্বংস করে দেয়। এই ধ্বংসপ্রক্রিয়া কেবল সামরিক বা রাজনৈতিক ছিল না, বরং এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক রূপান্তর, যা ইউরোপকে এক নতুন যুগে প্রবেশ করায়।
যুদ্ধক্ষেত্রে বর্বরদের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত সাফল্য আসে ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে অ্যাড্রিয়ানোপল যুদ্ধে। ভিসিগথরা রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং সম্রাট ভ্যালেন্সকে হত্যা করে। এই যুদ্ধে রোমান সামরিক শক্তির ওপর এক গভীর আঘাত আসে। এক দশকের মধ্যে তারা রোম নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অবশেষে, ৪১০ খ্রিস্টাব্দে অলারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথরা রোম নগরীতে প্রবেশ করে। প্রায় ৮০০ বছর পরে এই প্রথম রোম কোনও বিদেশি জাতির হাতে লুণ্ঠিত হয়। যদিও নগরী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি, তবুও এই লুণ্ঠন রোমান আত্মবিশ্বাসে চিরস্থায়ী আঘাত হানে।
এরপর আসে ভ্যান্ডালদের পালা। ৪৩৯ সালে তারা উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ শহর দখল করে, যা রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান খাদ্যশস্য সরবরাহ কেন্দ্র ছিল। এই ক্ষতি অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যকে চরম দুর্বল করে তোলে। ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান্ডালরা রোমে ঢুকে আরেকবার নগরী লুণ্ঠন করে, এবার আরো নির্মমভাবে। নগরের ধ্বংস, ঐতিহ্যবাহী মূর্তি ও স্থাপত্যের লুট, নারী ও শিশুদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া—সব মিলে এক মহাদুঃসময় নেমে আসে।
এদিকে, হুনদের নেতা আটিলা ইউরোপ জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে। যদিও রোম নগরী পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারেনি, তবুও তাদের আগমন বর্বরদের মধ্যে পুনর্গঠন সৃষ্টি করে। অনেক বর্বর গোষ্ঠী রোমের সঙ্গে সহযোগিতা করে হুনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ৪৫১ সালের ক্যাটালাউনিয়ান ফিল্ডস যুদ্ধ, যেখানে রোমান ও ভিসিগথ মিত্রবাহিনী আটিলাকে রুখে দেয়। তবে এই বিজয়ও রোমকে বাঁচাতে পারেনি, কারণ প্রতিটি সংঘর্ষের পর সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণভাবে ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে।
রোম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন জার্মান গোত্রভুক্ত সেনাপতি ওডোয়াসার পশ্চিম রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এটি ঐতিহাসিকভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতনের চূড়ান্ত মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। ওডোয়াসার নিজেকে ‘ইতালির রাজা’ ঘোষণা করেন, এবং রোমান সাম্রাজ্য একটি ইতিহাসে পরিণত হয়।
তবে এই পতন সম্পূর্ণ ধ্বংস হিসেবে দেখা সঠিক নয়। বরং বর্বরদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে। বর্বর শাসকরা রোমান প্রশাসন, আইন, সংস্কৃতি এবং খ্রিস্টধর্মের অনেক দিক নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে। গথরা স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে নিজেদের রাজ্য গঠন করে, ভ্যান্ডালরা আফ্রিকায়, ফ্র্যাঙ্করা গলে এবং লোম্বার্ডরা ইতালির উত্তরাংশে আধিপত্য বিস্তার করে। এই বর্বর রাজ্যগুলো ছিল পরবর্তী মধ্যযুগীয় ইউরোপের ভিত্তি।
এদিকে, রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ, অর্থাৎ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী করে আরো এক হাজার বছরের মতো টিকে থাকে। তারা রোমান ঐতিহ্য, খ্রিস্টীয় ভাবধারা এবং গ্রিক-রোমান সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে, যা রেনেসাঁ যুগ পর্যন্ত ইউরোপের চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলেছে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস এক দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে শুধু বাহ্যিক বর্বর আক্রমণ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক সংকটও সমানভাবে দায়ী ছিল। বর্বরদের অনুপ্রবেশ ছিল মূলত ফল, না যে তারা একদিনেই এসে রোমকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বরং রোম নিজেই ছিল অবক্ষয়প্রবণ, এবং বর্বররা ছিল সেই ধ্বংসপ্রক্রিয়ার ত্বরান্বিত শক্তি।
প্রথম দিকে বর্বরদের সঙ্গে রোমের সম্পর্ক ছিল দ্বৈত প্রকৃতির—কখনো তারা মিত্র, আবার কখনো শত্রু। রোমান শাসকগণ অনেক সময় বর্বরদের সেনাবাহিনী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই ‘ফোএডেরাটি’ ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে বর্বরদের আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলে। ফলত, এক সময় তারা শুধু রোমের সীমান্তে নয়, বরং কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।
আটিলা, অলারিক, ওডোয়াসারের মতো নেতারা ইতিহাসের পটভূমিতে একেকটি বিপ্লবী চরিত্র হয়ে ওঠে। তারা শুধু নগরী দখল করেনি, বরং এক প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে রেখেছে চিরস্থায়ী ছাপ। তবে বর্বররা রোমান সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেনি। বরং তারা তা নিজেদের মতো করে গ্রহণ করে ইউরোপের নতুন মানচিত্র তৈরি করেছে। ভিসিগথরা স্পেনে, ফ্র্যাঙ্করা গলে, ভ্যান্ডালরা আফ্রিকায় নতুন রাজ্য গঠন করে। এই রাজ্যগুলোর মাধ্যমে মধ্যযুগের ইউরোপের ভিত্তি গড়ে ওঠে।
রোমের পতন ছিল সভ্যতার পরিসমাপ্তি নয়, বরং পরিবর্তন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য প্রাচ্যে রোমান ঐতিহ্য বজায় রাখে এবং ইউরোপের নানা অংশে বর্বরদের সঙ্গে এক নতুন সংমিশ্রণ গড়ে ওঠে। মধ্যযুগ, রেনেসাঁ এবং অবশেষে আধুনিক ইউরোপের উত্থানের মধ্যে এই ইতিহাস এক অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে।
বর্বর অভিযানের ফলে আমরা বুঝতে পারি—কোনো সাম্রাজ্যই অমর নয়। শক্তি ও ঐশ্বর্যের শীর্ষে পৌঁছেও যদি নৈতিকতা, প্রশাসন ও সামাজিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়, তবে পতন এক অনিবার্য পরিণতি হয়ে ওঠে। ইতিহাস তাই কেবল অতীত নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা।
